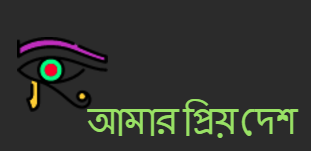কেন ‘লিওনার্দো দা ভিঞ্চি’ একজন বন্ড ভিলেন হবার জন্যে উপযুক্ত – ২য় পর্ব
আমরা জেনেছিলাম রেনেসাঁ যুগের ইতালিয়ান আবিষ্কারক লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কিছু তুলনামূলক ভাবে কম আলোচিত আবিষ্কারের কথা, যেগুলো তাকে যে কোনো বন্ড মুভিতে ভিলেনের রোল পাইয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। সত্যি কথা হলো, এমআই সিক্সের সব ফিউচারিস্টিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা এজেন্ট ‘জিরো জিরো সেভেন’ যদি মধ্যযুগে ভিঞ্চির এসব প্রযুক্তিগত আবিষ্কার দেখতো, তবে সেও নির্দ্বিধায় মূর্ছা যেতো। কারণ ভিঞ্চির কিছু কিছু আবিষ্কারের আইডিয়া এতই ফিউচারিস্টিক ছিলো যে সেগুলোকে বাস্তবে কার্যকর করতে আমাদের প্রায় চারশ’-পাঁচশ’ বছরের মতো সময় লেগে গেছে। যেমন বলা যায়-
৪। সাবমেরিন
আজকাল ‘মেরিন ওয়ারফেয়ার’ বা ‘পানির মধ্যে যুদ্ধের কলা-কৌশল’ জানা ছাড়া কোনো দেশেরই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা সম্ভব নয়। আর এই মেরিন ওয়ারফেয়ারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে সাবমেরিনের। কিন্তু এই সাবমেরিন কিছুকাল আগেও ছিলো শুধুমাত্র মানুষের কল্পনায়। উনিশ শতকের জুল ভার্ন রচিত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যসমূহে সাবমেরিনের কথা পড়ে সেই সময়ে অনেকেরই পিলে চমকে গিয়েছিলো। কপাল ভালো তারা পনেরশ’ শতকে জন্ম নেয়নি। কারণ, সেই সময়ে জন্ম নিলে হয়তো ভিঞ্চির আবিষ্কৃত সাবমেরিন দেখে তারা হার্ট অ্যাটাক করেই মারা যেতো।
ভিঞ্চির মূল ডিজাইন
ভিঞ্চির আমলে, তখন পর্যন্ত অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারা, ইতালির সবচেয়ে শক্তিশালী দুই সুপার-পাওয়ার ছিলো ‘ভেনিস’ এবং ‘জেনোয়া’। ভেনিস এবং জেনোয়া- উভয়েরই ছিলো অপ্রতিরোধ্য নৌ-বাহিনী। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কেউ এই দুই সুপার-পাওয়ারের সাথে অবস্থান করে টিকে থাকতে চাইলে সামনে রাস্তা খোলা ছিলো দুটো।
১। তাদের সব কথার প্রত্যুত্তরে “ইয়েস বস” বলা। অথবা,
২। তাদের সাথে সমান তালে ‘পাংগা’ নিতে সক্ষম নিজস্ব এক নৌ-বাহিনী থাকা।
কিন্তু সেই আমলে চলমান ক্রুসেডের ফলে ঘটা ক্ষয়ক্ষতির কারণে দ্বিতীয় পথ বেছে নেবার মত শক্তিমত্তা সম্পন্ন আর কেউ ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবশিষ্ট ছিলো না। তাই, তুর্কীরা এই দুর্বলতার সুযোগে বিশাল নৌবহর নিয়ে ইতালির উপকূলে উপস্থিত হবার আশংকায়, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন ‘মাস্টারমাইন্ড’ ভিঞ্চি। তিনি বানালেন নিচের ছবিতে উপস্থাপিত বস্তুটা।

জ্বি হ্যাঁ, এটা একটা সাবমেরিন যেটার মাথায় বসানো আছে দানবাকৃতির এক ধারালো ছুরির ফলা। ভিঞ্চি জানতেন, ভেনিস কিংবা জেনোয়ার বিশাল নৌ-বহরের সাথে জলের উপরিভাগে সামরিক শক্তি প্রদর্শন করতে যাওয়া আর খালি হাতে জলে নেমে কুমীরের সাথে কুস্তি করা একই জিনিস। দুনিয়াতে তো সবাই আর ‘এইস ভেঞ্চুরা’ নয়। তাই তিনি আগালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে। জলের নিচে দিয়ে। এরকম দু-চারটা সাবমেরিনই পুরো ভেনিস এবং জেনোয়ার নৌ-বহরের তলায় ফুটো করে দিয়ে তাদের সলিল সমাধি ঘটাতে যথেষ্ট ছিলো। সেই সাথে যথেষ্ট ছিলো মন্দিরে ‘পসাইডন’ দেবতার পাশে নিজের আরেকটা মূর্তি স্থাপন করে সেটার সামনে সবাইকে গড় হয়ে প্রণাম করাতে। কারণ উপস্থিত সবাই দেখতো- কোনো কারণ ছাড়াই একের পর এক যুদ্ধ জাহাজ পানির নিচে সিরিয়াল ধরে ডুবে যাচ্ছে।
কিন্তু বাকি আরো কিছু আবিষ্কারের মত ভিঞ্চি তার এই আবিষ্কারটার কথাও বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন- কী ভয়াবহ জিনিস তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ফলে তার মৃত্যুর পরে বারো ভলিউমের ‘কোডেক্স অ্যাটলান্টিকাস’ প্রকাশ হবার আগ পর্যন্ত কেউ কিসসু টের পায়নি এই আবিষ্কারের ব্যাপারে।
কতটুকু কার্যকরী ছিলো এই ডিজাইন?
ভিঞ্চির এই সাবমেরিনের কার্যকারিতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো প্রশ্নের উদয় হয়নি। এতেই বুঝা যায় কতটা নিখুঁত ছিলো তার এই ডিজাইন। কিন্তু একটা ব্যাপার। এই সাবমেরিন যারা চালাবে (টেকনিক্যালি দাঁড় বাইবে যারা) তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটায় কী চিন্তা করেছিলেন ভিঞ্চি? তারা অতল জলরাশিতে কীভাবে…………
.
.
.
উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ভিঞ্চির ডিজাইন করা ‘স্কুবা গিয়ার’। কোনো কারণে জাহাজ ধ্বংস না করে সেটা দখল নিতে চাইলে সৈন্যরা প্রথমে সাবমেরিন দিয়ে জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছাবে। তারপর ভিঞ্চির ডিজাইন করা এই ‘স্কুবা গিয়ার’ পরিহিত বিশেষ কমান্ডো বাহিনী অন্ধকারে জাহাজের ডেকে উঠে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে দখলে নিয়ে ফেলবে পুরো জাহাজ। যদিও আমাদের মতে- হামলা চালানো ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই বটে। শুধু এই গিয়ার পরে পানি হতে জাহাজের ডেকে উঠে আসলেই কাজ হয়ে যাবার কথা ছিলো বলে আমাদের বিশ্বাস। মধ্যযুগীয় কোনো সৈন্য এই মূর্তিমান আতংককে সামনাসামনি দেখেও যদি জাহাজ থেকে পানিতে লাফ না দেয়, তাহলে এর মানে দাঁড়ায় দুটো। হয় সে ইতোমধ্যেই মারা গেছে, না হয় ভয়ে জমে এতটাই বরফ হয়ে গেছে যে তার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই।
এই স্কুবা গিয়ারের ভেতরে অত্যন্ত জটিল সব ডিজাইন খুঁজে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সরলটা হলো ‘মূত্র সংরক্ষণকারী থলে’, যেটা বর্তমানের স্কুবা ডাইভারদের স্যুটের মাঝেও পাওয়া যায়। এটার কাজ হলো পানির নিচে ডাইভারকে উষ্ণতা প্রদানে সহায়তা করা। অর্থাৎ উনিশ শতকে মানুষ যখন সবে সাবমেরিন কল্পনায় দেখা শুরু করেছিলো, তার চারশ’ বছর আগেই ভিঞ্চি শুধু সাবমেরিনই বানিয়ে যাননি। তিনি সেই সাথে প্রতিষ্ঠা করে গেছিলেন তার নিজস্ব ‘নেভী সীল (Seal) বাহিনী’!
৫। ক্লাস্টার বোমা
কম পরিশ্রমে বহু সংখ্যক মানুষ নিধনে যখন মানবসভ্যতা নিত্য-নতুন উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তখন ২য় বিশ্বযুদ্ধের কিছু সময় আগে ক্লাস্টার বোমার আবির্ভাব। ক্লাস্টার বোমার মূলনীতি হলো “এক ঢিলে অনেক-অনেক পাখি”। এই বোমায় একটা শেলের ভেতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বোমা ভরে দেয়া থাকে। সেই শেল ছোঁড়া হলে সেটা মাটিতে পড়ার আগেই ফেটে যায়, আর ভিতরের ক্ষুদ্র বোমাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে চারপাশে। পরে সেগুলো আরেক দফায় বিস্ফোরণ ঘটায়। এরকম শুধু একটা শেল দিয়েই বিশাল এক এলাকা পুরো ধ্বসিয়ে দেয়া সম্ভব।
কথা হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীতে এসে ক্লাস্টার বোমা নিয়ে মানবসভ্যতা বেশ পুলক অনুভব করলেও ভিঞ্চি এই ভয়াবহ জিনিসটার আইডিয়া তৈরি করে গেছেন আরো ৫০০ বছর আগেই।
ভিঞ্চির মূল ডিজাইন
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ডের মধ্যেকার শতবর্ষ ব্যাপী (১৩৩৭-১৪৫৩) যুদ্ধে মধ্যযুগীয় রণকৌশলে আমূল পরিবর্তন চলে এসেছিলো। এই যুদ্ধের আগে ঘোড়সওয়ারী নাইটদের দুর্জেয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু পাঁচ প্রজন্ম ধরে চলা এই যুদ্ধে ঘোড়সওয়ারী নাইটেরা হয়ে পড়েছিলো পুরোপুরি অসহায়। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নাইটেরা যেখানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতো, সেখানে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড একই খরচে গড়ে তুলেছিলেন তিনগুণ বড় পদাতিক বাহিনী। তারা অতি হালকা বর্ম পরতো। তীরন্দাজ, পাইক ম্যান এবং ম্যান-অ্যাট-আর্মস এর সমন্বয়ে গড়ে তোলা বাহিনী হালকা বর্ম পরলেও যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেলো তারাই কার্যকর বেশি। একে তো তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলতে এবং অস্ত্র চালাতে পারে; তার উপর যে খরচে একটা নাইট বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেই একই খরচে তার তিনগুণ আয়তনের এই পদাতিক বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো। যেকোনো স্ট্রাটেজি ভিডিও গেমারকে জিজ্ঞেস করলেও তিনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন- নাইটদের নিকট ‘পাইক ম্যান-ম্যান অ্যাট আর্মস’ কম্বিনেশন কেন পুরো দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো!
যাই হোক, শতবর্ষ ব্যাপী এই যুদ্ধ হতে অন্যান্য দেশ নতুন রণকৌশল সম্পর্কে বেশ ভালোই শিক্ষা নিয়েছিলো। তারাও পাইকারি হারে পাইক-ম্যানদের নিয়ে বাহিনী গঠন করতে শুরু করে দিলো। ফলে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিলো, এই বিশাল সংখ্যক পদাতিক বাহিনীকে কীভাবে ঠেকানো যাবে? স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের অগণিত পদাতিক বাহিনীর সামনে ইতালি কীভাবে নিজেদের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য (যাদের অধিকাংশই বাইরের দেশ হতে ভাড়া করা) দিয়ে নিজেদের প্রাসাদ এবং দুর্গ প্রতিরক্ষা করবে? যথারীতি এগিয়ে এলেন ভিঞ্চি।

তিনি ডিজাইন করলেন এমন এক কামানের যেটার একশ গজের ভেতরে আসতে আসতেই শত্রুপক্ষের পুরো পদাতিক বাহিনী কচুকাটা হয়ে একটা সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত সংখ্যায় চলে আসবে। ইতালির শুধু প্রয়োজন হবে ক্ষুদ্র একটা দলের- যারা সেই কামানগুলোকে পাহারা দিবে, আর অনবরত এর ভেতরে ‘বিশেষ ধরণের গোলার’ জোগান দিবে। পরবর্তীতে বাকীরা গিয়ে সেই পদাতিক বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের শেষ করবে।
কতটুকু কার্যকরী ছিলো এই ডিজাইন?
ভিঞ্চির ডিজাইন করা কামানের প্রতিটা গোলার ভেতরে ভরে দেয়া ছিলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের টুকরো। যখন কামান হতে গোলাটা ছোঁড়া হতো, তখন সেই গোলাটা ফেটে যেতো আর পঙ্গপালের মত প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতো তীক্ষ্ম সব পাথরের টুকরো। ব্যাপারটাকে অনেকটা বলা যায় কোন যন্ত্র দিয়ে পাথরের টুকরো স্প্রে করার মত, যেখানে চূর্ণ করা টুকরোগুলো প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টির মতো এসে আঘাত হানতো শরীরে।
যারা এখনো বুঝতে পারছেন না এই কামানের ভয়াবহতা, তারা কখনো সুযোগ পেলে দু-চার মিনিট শিলা বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করুন।

৬। উড়ুক্কু যান
আকাশে উড়ার সাধ ছিলো মানুষের আজন্ম লালিত। সেই অনাদিকাল হতে কল্পনাবিলাসী মানুষ মাটিতে শুয়ে আকাশে পাখিদের ওড়া-উড়ি দেখতো আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। কিন্তু পাখিরা মানুষের মাথায় মলত্যাগ করে এই ব্যাপারটাই স্মরণ করিয়ে দিতো যে- আকাশের সীমানায় রাজত্ব শুধু তাদেরই, কোন মানুষের নয়। জবাবে অটো লিলিয়েনথেল এবং রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের মত বিজ্ঞানীরা কোমর বেঁধে নামলেন আকাশে মানুষের ক্ষমতা অধিষ্ঠিত করতে। তাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই আজ শুধু ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল নয়, মহাশূন্যেও মানুষের পদচারণা অতি নিয়মিত এক ব্যাপার।
কিন্তু কথা হলো, আকাশে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে লিলিয়েনথেল কিংবা রাইট ভাইদের মাধ্যমেই মানুষের পর্দায় আবির্ভাব ঘটেছিলো- একথা সত্যি নয়। বরং সফলভাবে এই রহস্য উদঘাটনে মানুষদের পর্দায় আবির্ভাব ঘটেছিলো সেই ভিঞ্চির আমলেই– পুরোপুরি ব্যাটম্যান স্টাইলে!

ভিঞ্চির মূল ডিজাইন
ভিঞ্চির রেখে যাওয়া সব নোট, খাতাপত্র এবং ডায়েরি ঘেঁটে তার বিভিন্ন প্রশ্ন ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে, সেটা হলো- কী করে মানুষের পক্ষে আকাশে উড়া সম্ভব? শুধু এই এক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই ভিঞ্চি তার জীবনের এক বড় অংশ ব্যয় করে ফেলেছিলেন। তার ডায়েরি এবং খাতার পাতার জায়গায় জায়গায় ভর্তি ছিলো ডানা মেলা পাখিদের নানারকম স্কেচে। তিনি পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বাদুড়দের উড়ার কৌশলকে। যার ফলাফল ছিলো নিম্নরূপ-
ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে ‘অর্নিথপ্টার (Ornithopter)’। এটাকে সাধারণ ‘গ্লাইডার’ এর মত ভাবলে ভুল করবেন। অর্নিথপ্টার ছিলো গ্লাইডারের থেকেও বেশী কিছু। এই যন্ত্রে পাইলট মাটির দিকে মুখ করে পুরো শরীর ভূমির সমান্তরালে রেখে অবস্থান গ্রহণ করতো। পায়ের কাছে ছিলো একজোড়া পেডাল। সেই পেডাল রড এবং পুলি সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলো যন্ত্রটার দুই ডানার সাথে। যখন পা দিয়ে পেডাল ঘোরানো হতো, তখন পাখিদের ডানা ঝাপটানোর মত করে যন্ত্রটার দুই ডানা উপরে-নিচে সমানে ঝাপটে চলতো।
এক ডানা হতে আরেক ডানা পর্যন্ত পুরো যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য ছিলো ৩৩ ফুট। যন্ত্রে বিভিন্ন কাঠের ফ্রেমগুলো বানানো হয়েছিলো পাইন গাছের মত হালকা কিন্তু দৃঢ় কাঠ দিয়ে। কাপড়ের অংশে ব্যবহৃত হয়েছিলো সিল্কের কাপড়। পায়ের কাছে পেডালের সাথে সাথে হাতের কাছেও ক্র্যাঙ্কের (Crank) এর মত একটা বস্তু ছিলো, যেটার ভূমিকা ছিলো অনেকটা গিয়ারের মত। অর্থাৎ ক্র্যাঙ্কটা ঘুরিয়ে যন্ত্রের ডানা-ঝাপটানোর হার বাড়ানো-কমানো যেতো। আর উড়ার সময় দিক নির্দেশ করার জন্যে মাথার কাছে ছিলো আরেকটা বিশেষ ‘হেড পিস’।
কতটুকু কার্যকরী ছিলো এই ডিজাইন?
এই যন্ত্রের সমস্যা ছিলো একটাই। ভূমি হতে আকাশে উড্ডয়ন। উঁচু পাহাড় বা বিল্ডিং এর ছাদ হতে যন্ত্রটা নিয়ে লাফিয়ে পড়া ছাড়া এটাকে বাতাসে ভাসানোর আর কোন উপায় ছিলো না। কিন্তু কোনক্রমে একবার বাতাসে ভাসাতে পারলেই যন্ত্রটা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে বেড়ানো যেতো। অর্থাৎ, যন্ত্রটা আকাশে উড়ার ক্ষেত্রে সফল হলেও প্রাথমিকভাবে ভূমি হতে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিপক্ষে গিয়ে আকাশে উড্ডয়ন করানোর মত যথেষ্ট শক্তির যোগান দেয়া সম্ভব হয়নি এই যন্ত্রটাতে। এর প্রথম কারণ ছিলো, সেই সময়কার প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা। আর দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো, এই যন্ত্রটা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে সাহসী ভলান্টিয়ারের অভাব। ফলে ভিঞ্চিকে যন্ত্রটার এই আপাত কিছু গুণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো………এবং না, পরে কোনো চোরেদের সংগঠন জাতীয় কিছুর সহায়তায়ও এই যন্ত্রের পরীক্ষণে ভিঞ্চি আর উৎসাহী হননি।
কিন্তু তারপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। যদি কোনভাবে পাইলটের জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের প্রয়োজন হয়- তাহলে? মানে ধরুন, কোনোভাবে আকাশে উড়ার সময় যন্ত্রটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর……
.
.
.
.
উপরের ছবিতে দেখছেন ভিঞ্চির ডিজাইন করা প্যারাসুট। আধুনিক প্যারাসুটের সাথে এর তফাৎ ছিলো- আধুনিক প্যারাসুট ভিঞ্চিরটার মত পিরামিড আকৃতিবিশিষ্ট নয়। ফলে অনেক ‘অ্যারোডায়নামিক্স’ বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছিলেন- এটা বাতাসের বাধাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে কোনো মানুষকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে এবং নিরাপদ অবতরণ করাতে সক্ষম হবে না। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে ‘ডেয়ার ডেভিল’ নামে খ্যাত ব্রিটিশ স্কাই-ডাইভার ‘অ্যাড্রিয়ান নিকোলাস’ ২০০০ সালে হুবহু একই ধরনের একটা প্যারাসুট বানান আর ১০,০০০ ফুট উঁচুতে থাকা বেলুন হতে লাফ দেন। ৭,০০০ ফুট উচ্চতায় নেমে আসার পরে তিনি তার সেই প্যারাসুট খুলেন এবং তথাকথিত ‘অ্যারোডায়নামিক্স’ বিশেষজ্ঞদের মুখে ছাই ঢেলে নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করেন।

পরবর্তীতে তিনি মিডিয়াকে জানিয়েছিলেন– ভিঞ্চির ডিজাইন করা প্যারাসুটের মাধ্যমে “আধুনিক প্যারাসুটের চেয়েও অনেক মসৃণভাবে” তিনি মাটিতে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি এটাও বলেছিলেন, “It took one of the greatest minds who ever lived to design it, but it took 500 years to find a man with a brain small enough to actually go and fly it”.
উৎস ঃ https://bigganjatra.org/vinci_as_bond_villain_02/
৪। সাবমেরিন
আজকাল ‘মেরিন ওয়ারফেয়ার’ বা ‘পানির মধ্যে যুদ্ধের কলা-কৌশল’ জানা ছাড়া কোনো দেশেরই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা সম্ভব নয়। আর এই মেরিন ওয়ারফেয়ারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে সাবমেরিনের। কিন্তু এই সাবমেরিন কিছুকাল আগেও ছিলো শুধুমাত্র মানুষের কল্পনায়। উনিশ শতকের জুল ভার্ন রচিত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যসমূহে সাবমেরিনের কথা পড়ে সেই সময়ে অনেকেরই পিলে চমকে গিয়েছিলো। কপাল ভালো তারা পনেরশ’ শতকে জন্ম নেয়নি। কারণ, সেই সময়ে জন্ম নিলে হয়তো ভিঞ্চির আবিষ্কৃত সাবমেরিন দেখে তারা হার্ট অ্যাটাক করেই মারা যেতো।
ভিঞ্চির মূল ডিজাইন
ভিঞ্চির আমলে, তখন পর্যন্ত অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারা, ইতালির সবচেয়ে শক্তিশালী দুই সুপার-পাওয়ার ছিলো ‘ভেনিস’ এবং ‘জেনোয়া’। ভেনিস এবং জেনোয়া- উভয়েরই ছিলো অপ্রতিরোধ্য নৌ-বাহিনী। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কেউ এই দুই সুপার-পাওয়ারের সাথে অবস্থান করে টিকে থাকতে চাইলে সামনে রাস্তা খোলা ছিলো দুটো।
১। তাদের সব কথার প্রত্যুত্তরে “ইয়েস বস” বলা। অথবা,
২। তাদের সাথে সমান তালে ‘পাংগা’ নিতে সক্ষম নিজস্ব এক নৌ-বাহিনী থাকা।
কিন্তু সেই আমলে চলমান ক্রুসেডের ফলে ঘটা ক্ষয়ক্ষতির কারণে দ্বিতীয় পথ বেছে নেবার মত শক্তিমত্তা সম্পন্ন আর কেউ ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবশিষ্ট ছিলো না। তাই, তুর্কীরা এই দুর্বলতার সুযোগে বিশাল নৌবহর নিয়ে ইতালির উপকূলে উপস্থিত হবার আশংকায়, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন ‘মাস্টারমাইন্ড’ ভিঞ্চি। তিনি বানালেন নিচের ছবিতে উপস্থাপিত বস্তুটা।

জ্বি হ্যাঁ, এটা একটা সাবমেরিন যেটার মাথায় বসানো আছে দানবাকৃতির এক ধারালো ছুরির ফলা। ভিঞ্চি জানতেন, ভেনিস কিংবা জেনোয়ার বিশাল নৌ-বহরের সাথে জলের উপরিভাগে সামরিক শক্তি প্রদর্শন করতে যাওয়া আর খালি হাতে জলে নেমে কুমীরের সাথে কুস্তি করা একই জিনিস। দুনিয়াতে তো সবাই আর ‘এইস ভেঞ্চুরা’ নয়। তাই তিনি আগালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে। জলের নিচে দিয়ে। এরকম দু-চারটা সাবমেরিনই পুরো ভেনিস এবং জেনোয়ার নৌ-বহরের তলায় ফুটো করে দিয়ে তাদের সলিল সমাধি ঘটাতে যথেষ্ট ছিলো। সেই সাথে যথেষ্ট ছিলো মন্দিরে ‘পসাইডন’ দেবতার পাশে নিজের আরেকটা মূর্তি স্থাপন করে সেটার সামনে সবাইকে গড় হয়ে প্রণাম করাতে। কারণ উপস্থিত সবাই দেখতো- কোনো কারণ ছাড়াই একের পর এক যুদ্ধ জাহাজ পানির নিচে সিরিয়াল ধরে ডুবে যাচ্ছে।
কিন্তু বাকি আরো কিছু আবিষ্কারের মত ভিঞ্চি তার এই আবিষ্কারটার কথাও বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন- কী ভয়াবহ জিনিস তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ফলে তার মৃত্যুর পরে বারো ভলিউমের ‘কোডেক্স অ্যাটলান্টিকাস’ প্রকাশ হবার আগ পর্যন্ত কেউ কিসসু টের পায়নি এই আবিষ্কারের ব্যাপারে।
কতটুকু কার্যকরী ছিলো এই ডিজাইন?
ভিঞ্চির এই সাবমেরিনের কার্যকারিতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো প্রশ্নের উদয় হয়নি। এতেই বুঝা যায় কতটা নিখুঁত ছিলো তার এই ডিজাইন। কিন্তু একটা ব্যাপার। এই সাবমেরিন যারা চালাবে (টেকনিক্যালি দাঁড় বাইবে যারা) তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটায় কী চিন্তা করেছিলেন ভিঞ্চি? তারা অতল জলরাশিতে কীভাবে…………
.
.
.
উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ভিঞ্চির ডিজাইন করা ‘স্কুবা গিয়ার’। কোনো কারণে জাহাজ ধ্বংস না করে সেটা দখল নিতে চাইলে সৈন্যরা প্রথমে সাবমেরিন দিয়ে জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছাবে। তারপর ভিঞ্চির ডিজাইন করা এই ‘স্কুবা গিয়ার’ পরিহিত বিশেষ কমান্ডো বাহিনী অন্ধকারে জাহাজের ডেকে উঠে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে দখলে নিয়ে ফেলবে পুরো জাহাজ। যদিও আমাদের মতে- হামলা চালানো ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই বটে। শুধু এই গিয়ার পরে পানি হতে জাহাজের ডেকে উঠে আসলেই কাজ হয়ে যাবার কথা ছিলো বলে আমাদের বিশ্বাস। মধ্যযুগীয় কোনো সৈন্য এই মূর্তিমান আতংককে সামনাসামনি দেখেও যদি জাহাজ থেকে পানিতে লাফ না দেয়, তাহলে এর মানে দাঁড়ায় দুটো। হয় সে ইতোমধ্যেই মারা গেছে, না হয় ভয়ে জমে এতটাই বরফ হয়ে গেছে যে তার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই।
এই স্কুবা গিয়ারের ভেতরে অত্যন্ত জটিল সব ডিজাইন খুঁজে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সরলটা হলো ‘মূত্র সংরক্ষণকারী থলে’, যেটা বর্তমানের স্কুবা ডাইভারদের স্যুটের মাঝেও পাওয়া যায়। এটার কাজ হলো পানির নিচে ডাইভারকে উষ্ণতা প্রদানে সহায়তা করা। অর্থাৎ উনিশ শতকে মানুষ যখন সবে সাবমেরিন কল্পনায় দেখা শুরু করেছিলো, তার চারশ’ বছর আগেই ভিঞ্চি শুধু সাবমেরিনই বানিয়ে যাননি। তিনি সেই সাথে প্রতিষ্ঠা করে গেছিলেন তার নিজস্ব ‘নেভী সীল (Seal) বাহিনী’!
৫। ক্লাস্টার বোমা
কম পরিশ্রমে বহু সংখ্যক মানুষ নিধনে যখন মানবসভ্যতা নিত্য-নতুন উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তখন ২য় বিশ্বযুদ্ধের কিছু সময় আগে ক্লাস্টার বোমার আবির্ভাব। ক্লাস্টার বোমার মূলনীতি হলো “এক ঢিলে অনেক-অনেক পাখি”। এই বোমায় একটা শেলের ভেতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বোমা ভরে দেয়া থাকে। সেই শেল ছোঁড়া হলে সেটা মাটিতে পড়ার আগেই ফেটে যায়, আর ভিতরের ক্ষুদ্র বোমাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে চারপাশে। পরে সেগুলো আরেক দফায় বিস্ফোরণ ঘটায়। এরকম শুধু একটা শেল দিয়েই বিশাল এক এলাকা পুরো ধ্বসিয়ে দেয়া সম্ভব।
কথা হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীতে এসে ক্লাস্টার বোমা নিয়ে মানবসভ্যতা বেশ পুলক অনুভব করলেও ভিঞ্চি এই ভয়াবহ জিনিসটার আইডিয়া তৈরি করে গেছেন আরো ৫০০ বছর আগেই।
ভিঞ্চির মূল ডিজাইন
ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ডের মধ্যেকার শতবর্ষ ব্যাপী (১৩৩৭-১৪৫৩) যুদ্ধে মধ্যযুগীয় রণকৌশলে আমূল পরিবর্তন চলে এসেছিলো। এই যুদ্ধের আগে ঘোড়সওয়ারী নাইটদের দুর্জেয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু পাঁচ প্রজন্ম ধরে চলা এই যুদ্ধে ঘোড়সওয়ারী নাইটেরা হয়ে পড়েছিলো পুরোপুরি অসহায়। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নাইটেরা যেখানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতো, সেখানে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড একই খরচে গড়ে তুলেছিলেন তিনগুণ বড় পদাতিক বাহিনী। তারা অতি হালকা বর্ম পরতো। তীরন্দাজ, পাইক ম্যান এবং ম্যান-অ্যাট-আর্মস এর সমন্বয়ে গড়ে তোলা বাহিনী হালকা বর্ম পরলেও যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেলো তারাই কার্যকর বেশি। একে তো তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলতে এবং অস্ত্র চালাতে পারে; তার উপর যে খরচে একটা নাইট বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেই একই খরচে তার তিনগুণ আয়তনের এই পদাতিক বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো। যেকোনো স্ট্রাটেজি ভিডিও গেমারকে জিজ্ঞেস করলেও তিনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন- নাইটদের নিকট ‘পাইক ম্যান-ম্যান অ্যাট আর্মস’ কম্বিনেশন কেন পুরো দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো!
যাই হোক, শতবর্ষ ব্যাপী এই যুদ্ধ হতে অন্যান্য দেশ নতুন রণকৌশল সম্পর্কে বেশ ভালোই শিক্ষা নিয়েছিলো। তারাও পাইকারি হারে পাইক-ম্যানদের নিয়ে বাহিনী গঠন করতে শুরু করে দিলো। ফলে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিলো, এই বিশাল সংখ্যক পদাতিক বাহিনীকে কীভাবে ঠেকানো যাবে? স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের অগণিত পদাতিক বাহিনীর সামনে ইতালি কীভাবে নিজেদের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য (যাদের অধিকাংশই বাইরের দেশ হতে ভাড়া করা) দিয়ে নিজেদের প্রাসাদ এবং দুর্গ প্রতিরক্ষা করবে? যথারীতি এগিয়ে এলেন ভিঞ্চি।

তিনি ডিজাইন করলেন এমন এক কামানের যেটার একশ গজের ভেতরে আসতে আসতেই শত্রুপক্ষের পুরো পদাতিক বাহিনী কচুকাটা হয়ে একটা সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত সংখ্যায় চলে আসবে। ইতালির শুধু প্রয়োজন হবে ক্ষুদ্র একটা দলের- যারা সেই কামানগুলোকে পাহারা দিবে, আর অনবরত এর ভেতরে ‘বিশেষ ধরণের গোলার’ জোগান দিবে। পরবর্তীতে বাকীরা গিয়ে সেই পদাতিক বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের শেষ করবে।
কতটুকু কার্যকরী ছিলো এই ডিজাইন?
ভিঞ্চির ডিজাইন করা কামানের প্রতিটা গোলার ভেতরে ভরে দেয়া ছিলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের টুকরো। যখন কামান হতে গোলাটা ছোঁড়া হতো, তখন সেই গোলাটা ফেটে যেতো আর পঙ্গপালের মত প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতো তীক্ষ্ম সব পাথরের টুকরো। ব্যাপারটাকে অনেকটা বলা যায় কোন যন্ত্র দিয়ে পাথরের টুকরো স্প্রে করার মত, যেখানে চূর্ণ করা টুকরোগুলো প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টির মতো এসে আঘাত হানতো শরীরে।
যারা এখনো বুঝতে পারছেন না এই কামানের ভয়াবহতা, তারা কখনো সুযোগ পেলে দু-চার মিনিট শিলা বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করুন।

৬। উড়ুক্কু যান
আকাশে উড়ার সাধ ছিলো মানুষের আজন্ম লালিত। সেই অনাদিকাল হতে কল্পনাবিলাসী মানুষ মাটিতে শুয়ে আকাশে পাখিদের ওড়া-উড়ি দেখতো আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। কিন্তু পাখিরা মানুষের মাথায় মলত্যাগ করে এই ব্যাপারটাই স্মরণ করিয়ে দিতো যে- আকাশের সীমানায় রাজত্ব শুধু তাদেরই, কোন মানুষের নয়। জবাবে অটো লিলিয়েনথেল এবং রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের মত বিজ্ঞানীরা কোমর বেঁধে নামলেন আকাশে মানুষের ক্ষমতা অধিষ্ঠিত করতে। তাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই আজ শুধু ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল নয়, মহাশূন্যেও মানুষের পদচারণা অতি নিয়মিত এক ব্যাপার।
কিন্তু কথা হলো, আকাশে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে লিলিয়েনথেল কিংবা রাইট ভাইদের মাধ্যমেই মানুষের পর্দায় আবির্ভাব ঘটেছিলো- একথা সত্যি নয়। বরং সফলভাবে এই রহস্য উদঘাটনে মানুষদের পর্দায় আবির্ভাব ঘটেছিলো সেই ভিঞ্চির আমলেই– পুরোপুরি ব্যাটম্যান স্টাইলে!

ভিঞ্চির মূল ডিজাইন
ভিঞ্চির রেখে যাওয়া সব নোট, খাতাপত্র এবং ডায়েরি ঘেঁটে তার বিভিন্ন প্রশ্ন ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে, সেটা হলো- কী করে মানুষের পক্ষে আকাশে উড়া সম্ভব? শুধু এই এক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই ভিঞ্চি তার জীবনের এক বড় অংশ ব্যয় করে ফেলেছিলেন। তার ডায়েরি এবং খাতার পাতার জায়গায় জায়গায় ভর্তি ছিলো ডানা মেলা পাখিদের নানারকম স্কেচে। তিনি পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বাদুড়দের উড়ার কৌশলকে। যার ফলাফল ছিলো নিম্নরূপ-
ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে ‘অর্নিথপ্টার (Ornithopter)’। এটাকে সাধারণ ‘গ্লাইডার’ এর মত ভাবলে ভুল করবেন। অর্নিথপ্টার ছিলো গ্লাইডারের থেকেও বেশী কিছু। এই যন্ত্রে পাইলট মাটির দিকে মুখ করে পুরো শরীর ভূমির সমান্তরালে রেখে অবস্থান গ্রহণ করতো। পায়ের কাছে ছিলো একজোড়া পেডাল। সেই পেডাল রড এবং পুলি সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলো যন্ত্রটার দুই ডানার সাথে। যখন পা দিয়ে পেডাল ঘোরানো হতো, তখন পাখিদের ডানা ঝাপটানোর মত করে যন্ত্রটার দুই ডানা উপরে-নিচে সমানে ঝাপটে চলতো।
এক ডানা হতে আরেক ডানা পর্যন্ত পুরো যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য ছিলো ৩৩ ফুট। যন্ত্রে বিভিন্ন কাঠের ফ্রেমগুলো বানানো হয়েছিলো পাইন গাছের মত হালকা কিন্তু দৃঢ় কাঠ দিয়ে। কাপড়ের অংশে ব্যবহৃত হয়েছিলো সিল্কের কাপড়। পায়ের কাছে পেডালের সাথে সাথে হাতের কাছেও ক্র্যাঙ্কের (Crank) এর মত একটা বস্তু ছিলো, যেটার ভূমিকা ছিলো অনেকটা গিয়ারের মত। অর্থাৎ ক্র্যাঙ্কটা ঘুরিয়ে যন্ত্রের ডানা-ঝাপটানোর হার বাড়ানো-কমানো যেতো। আর উড়ার সময় দিক নির্দেশ করার জন্যে মাথার কাছে ছিলো আরেকটা বিশেষ ‘হেড পিস’।
কতটুকু কার্যকরী ছিলো এই ডিজাইন?
এই যন্ত্রের সমস্যা ছিলো একটাই। ভূমি হতে আকাশে উড্ডয়ন। উঁচু পাহাড় বা বিল্ডিং এর ছাদ হতে যন্ত্রটা নিয়ে লাফিয়ে পড়া ছাড়া এটাকে বাতাসে ভাসানোর আর কোন উপায় ছিলো না। কিন্তু কোনক্রমে একবার বাতাসে ভাসাতে পারলেই যন্ত্রটা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে বেড়ানো যেতো। অর্থাৎ, যন্ত্রটা আকাশে উড়ার ক্ষেত্রে সফল হলেও প্রাথমিকভাবে ভূমি হতে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিপক্ষে গিয়ে আকাশে উড্ডয়ন করানোর মত যথেষ্ট শক্তির যোগান দেয়া সম্ভব হয়নি এই যন্ত্রটাতে। এর প্রথম কারণ ছিলো, সেই সময়কার প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা। আর দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো, এই যন্ত্রটা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে সাহসী ভলান্টিয়ারের অভাব। ফলে ভিঞ্চিকে যন্ত্রটার এই আপাত কিছু গুণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো………এবং না, পরে কোনো চোরেদের সংগঠন জাতীয় কিছুর সহায়তায়ও এই যন্ত্রের পরীক্ষণে ভিঞ্চি আর উৎসাহী হননি।
কিন্তু তারপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। যদি কোনভাবে পাইলটের জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের প্রয়োজন হয়- তাহলে? মানে ধরুন, কোনোভাবে আকাশে উড়ার সময় যন্ত্রটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর……
.
.
.
.
উপরের ছবিতে দেখছেন ভিঞ্চির ডিজাইন করা প্যারাসুট। আধুনিক প্যারাসুটের সাথে এর তফাৎ ছিলো- আধুনিক প্যারাসুট ভিঞ্চিরটার মত পিরামিড আকৃতিবিশিষ্ট নয়। ফলে অনেক ‘অ্যারোডায়নামিক্স’ বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছিলেন- এটা বাতাসের বাধাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে কোনো মানুষকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে এবং নিরাপদ অবতরণ করাতে সক্ষম হবে না। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে ‘ডেয়ার ডেভিল’ নামে খ্যাত ব্রিটিশ স্কাই-ডাইভার ‘অ্যাড্রিয়ান নিকোলাস’ ২০০০ সালে হুবহু একই ধরনের একটা প্যারাসুট বানান আর ১০,০০০ ফুট উঁচুতে থাকা বেলুন হতে লাফ দেন। ৭,০০০ ফুট উচ্চতায় নেমে আসার পরে তিনি তার সেই প্যারাসুট খুলেন এবং তথাকথিত ‘অ্যারোডায়নামিক্স’ বিশেষজ্ঞদের মুখে ছাই ঢেলে নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করেন।

পরবর্তীতে তিনি মিডিয়াকে জানিয়েছিলেন– ভিঞ্চির ডিজাইন করা প্যারাসুটের মাধ্যমে “আধুনিক প্যারাসুটের চেয়েও অনেক মসৃণভাবে” তিনি মাটিতে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি এটাও বলেছিলেন, “It took one of the greatest minds who ever lived to design it, but it took 500 years to find a man with a brain small enough to actually go and fly it”.
উৎস ঃ https://bigganjatra.org/vinci_as_bond_villain_02/