স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু : মুক্ত দর্শনের বিজ্ঞানী
 মে ১০, ১৯০১। লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় মিলনায়তন। দীর্ঘদিন এখানে এত লোকের ভিড়ে কোনো বিজ্ঞানী বক্তব্য দেননি। এই বিজ্ঞানী আবার এসেছেন সাত সাগরের ওপার অর্থাত্ ভারত থেকে। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন লর্ড রেইলির মতো বিজ্ঞানকুল শিরোমণি। দর্শকেরা অবশ্য খুব বেশি চমত্কৃত হলেন না পরীক্ষার বন্দোবস্ত দেখে। একটি গাছের মূল একটি বোতলের পানির মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা, গাছ থেকে কী সব তারটার টেনে এটা কিম্ভূতদর্শন যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো।
মে ১০, ১৯০১। লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় মিলনায়তন। দীর্ঘদিন এখানে এত লোকের ভিড়ে কোনো বিজ্ঞানী বক্তব্য দেননি। এই বিজ্ঞানী আবার এসেছেন সাত সাগরের ওপার অর্থাত্ ভারত থেকে। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন লর্ড রেইলির মতো বিজ্ঞানকুল শিরোমণি। দর্শকেরা অবশ্য খুব বেশি চমত্কৃত হলেন না পরীক্ষার বন্দোবস্ত দেখে। একটি গাছের মূল একটি বোতলের পানির মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা, গাছ থেকে কী সব তারটার টেনে এটা কিম্ভূতদর্শন যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো।দর্শকদের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞানী জানালেন, বোতলের ভেতরের তরল পদার্থটি পানি নয়, এটি ব্রোমাইড সলিউশন। উপস্থিত বিজ্ঞানের লোকেরা বুঝলেন অচিরেই গাছটি মরবে। কারণ, হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের এই লবণের দ্রবণ সহ্য করার ক্ষমতা গাছের নেই। তাতে অবশ্য তাঁদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁদের লক্ষ্য কিম্ভূত যন্ত্রটি।
বিজ্ঞানী গাছের মূলকে সলিউশনে দিয়ে দিলেন আর চালু করে দিলেন তাঁর যন্ত্র। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি কাগজের ওপর মানুষের হূদ্যন্ত্রের ওঠা-নামার মতো গ্রাফ আঁকতে শুরু করল। তবে সেটিতে তেমন কোনো চাঞ্চল্য নেই। পেন্ডুলামের মতো একই নিয়মের ওঠা-নামা। কিন্তু একটু পরই যন্ত্রের গ্রাফে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিল। গ্রাফ বেশ দ্রুত ওঠা-নামা শুরু করল। মনে হচ্ছে কার সঙ্গে যেন লড়ছে গাছটি। তবে একসময় সব চাঞ্চল্য থেমে গেল।
উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা দেখলেন, গাছটি মরে গেছে!
উপস্থিত বিজ্ঞানী ও দর্শকেরা সবাই চমত্কৃত হলেন ভারতীয় বাঙালি বিজ্ঞানীর এই যন্ত্রে। লর্ড রেইলি উঠে গিয়ে দর্শক সারিতে বসা বিজ্ঞানীর স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে এলেন।
উদ্ভিদেরও প্রাণীদের মতো প্রাণ আছে, এই ধারণা কিন্তু নতুন নয়। কারণ, সবাই দেখেছে বীজ থেকে চারা হয়, সেটি মহিরুহ হয় এবং একসময় মরে যায়। কিন্তু উদ্দীপনায় উদ্ভিদও প্রাণীর মতো প্রতিক্রিয়া করে, জোর করে মেরে ফেলা হলে আর্তচিত্কার করে—এমনটা কেউ এর আগে ভাবেননি। ভেবেছেন ওই বাঙালি বিজ্ঞানী।
মুন্সিগঞ্জের রাঢ়িখালের সন্তান জগদীশ চন্দ্র বসু। ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবান চন্দ্র বসু ও বনসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তান। জগদীশের জন্মের সময় তাঁর বাবা ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। তবে জগদীশ চন্দ্রের জন্ম ময়মনসিংহে, নানার বাড়িতে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। সে সময় ইংরেজদের স্কুলে ছেলেমেয়েকে পড়ানো ছিল আভিজাত্যের ব্যাপার। কিন্তু ভগবান চন্দ্র বসু তাঁর সন্তানকে এমনকি ফরিদপুরেও রাখলেন না, পাঠিয়ে দিলেন নিজ গ্রামে। সেখানে বাবার চালু করা পাঠশালায় জগদীশের পড়ালেখার হাতেখড়ি। প্রাথমিক পড়ালেখার পর ফরিদপুর হাইস্কুলে পড়ে অবশেষে ১৮৬৯ সালে জগদীশ চলে গেলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ও কলেজে। সেখানে তখন বিজ্ঞান নিয়ে ভারতবাসীকে জাগানোর চেষ্টা করছেন ফাদার ইউজিন ল্যাকো। বিজ্ঞানেই মুক্তি, এ ছিল তাঁর যুক্তি। জগদীশ হয়ে উঠলেন তাঁর ভক্ত।
১৮৭৯ সালে ফিজিক্যাল সায়েন্সে জগদীশ চন্দ্র বিএ পাস করলেন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেখা করার জন্য তিনি বিলাত (ইংল্যান্ড) যাওয়ার মনস্থির করলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর মা। কারণ, তার কিছুদিন আগে মাত্র ১০ বছর বয়সে জগদীশের ছোট ভাই মারা যায়। মায়ের মন অবশিষ্ট সন্তান সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লন্ডন যাক, এটি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। অন্যদিকে, ভগবান চন্দ্র বসু অসুস্থ হয়ে পড়ায় বলতে গেলে ঘরবসা। আধা মাইনেতে চলেন। যেসব উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন গ্রামের মানুষদের জন্য তার বেশির ভাগই ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অনেক ঋণে জর্জরিত। মন খারাপ করে জগদীশ দেশেই থাকবেন বলে যখন সিদ্ধান্ত নেন তখন আবার মায়ের মন পরিবর্তন হয়। বনসুন্দরী দেবী নিজের গয়না বিক্রি করে ও তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ছেলেকে ডাক্তারি পড়ার জন্য বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জগদীশ আক্রান্ত হলেন জ্বরে, শরীর হয়ে গেল দুর্বল। বোঝা গেল ডাক্তারি পড়াটা কঠিন হয়ে যাবে।
এই সময় জগদীশের স্ত্রীর ভাই বাংলার প্রথম রেংলার, আনন্দ মোহন বসু জগদীশকে কেমব্রিজে ভর্তি হতে সহায়তা করেন। আনন্দ মোহন বসু ১৮৭৪ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে গণিতে ট্রাইপস পান। কেমব্রিজে আর লন্ডনে জগদীশের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন লর্ড রেইলি, মাইকেল ফস্টার, সিডনি ভাইন, ফ্রান্সিস ডারউইনের মতো বিজ্ঞানীরা। ১৮৮৪ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারত ফিরে আসেন। দেশে ফিরে একই বছরে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে চাকরিতে যোগদানের চেষ্টা করেন। ‘ভারতীয়রা পড়াতে পারে না’ অজুহাতে কলেজের সেই সময়কার অধ্যক্ষ চার্লস টাউনি এবং বাংলার পাবলিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্যার আলফ্রেড ক্রফট প্রবল বিরোধিতা করলে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপনের শরণাপন্ন হন। শেষমেশ, ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে তিনি শিক্ষক হলেও চার্লস টাউনি এবং স্যার আলফ্রেড ক্রফট তাঁকে ‘অস্থায়ীভাবে’ নিয়োগ দেন। এমনকি তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হয় একই পদে আসীন ব্রিটিশ অধ্যাপকদের অর্ধেক। এমনকি তাঁকে গবেষণাগারে একটা কাজ করারও সুযোগ দেওয়া হতো না। সাহসী জগদীশ অর্ধেক বেতনের নিয়োগপত্র অগ্রাহ্য করে কলেজে যোগ দেন এবং একনাগাড়ে তিন বছর বেতন নিতে অস্বীকার করেন। এই সময়কালে নিজের মেধা ও পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি প্রায় সবার মন জয় করেন। অন্যদিকে নিজের বাড়িতেও একটি গবেষণাগার গড়ে তোলেন। তিন বছর পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সসম্মানে, পূর্ণবেতনে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। আর এই নিয়োগ দেওয়া হয় ভূতাপেক্ষা, অর্থাত্ তিন বছর আগে থেকে। তাঁর তিন বছরের বকেয়া বেতনও পরিশোধ করা হয়। সেই টাকা দিয়ে জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর বাবার ঋণ শোধ করেন। সেই সময়ে জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণার আগ্রহের বিষয়বস্তু ছিল ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, যা মাইক্রোওয়েভ নামে পরিচিত। সে সময় তিনি ‘কোহেরার’ নামে একটি ধারণাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে দেখেন সেটিকে মাইক্রোতরঙ্গের গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১৮৯৪ সালে তিনি কলকাতায় প্রথম বিনা তারে বার্তা প্রেরণ এবং তা গ্রহণ করার একটি কৌশল দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। বড় লাটের হস্তক্ষেপে তাঁর এই আবিষ্কার ইংল্যান্ডে দেখানোর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহায়তা করলে তিনি লন্ডনে গিয়ে সেটি প্রদর্শন করেন। ১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই লন্ডনে রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতিতে তিনি তাঁর আবিষ্কার সব বিজ্ঞানীর সামনে তুলে ধরেন। এমনকি তিনি তাঁর পরীক্ষার খুঁটিনাটি এত বিশদভাবে তুলে ধরেন যে তা থেকে যে কেউ পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।
মানবসভ্যতার ইতিহাসে কলকাতার সেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের ঘটনাটিই প্রথম। পরে লন্ডনেও তিনি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর উদ্ভাবনের কোনো ‘পেটেন্ট’ বা ‘স্বত্ব’ করেননি। কারণ, কর্ণ ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর সব কাজকর্ম হবে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। বলা যায়, জগদীশ চন্দ্র বসু হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম মুক্ত দর্শনের অধিকারী বিজ্ঞানী।
লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর পদার্থবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এর অন্যতম কারণ হলো, তিনি তখন ‘ধাতব বস্তুর’ প্রাণ আছে কি না তা ভাবতে থাকেন। তবে তাঁর এই ভাবনাটা ক্রমেই উদ্ভিদের দিকেই চলে যায়।
ফলে মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জগদীশের সাফল্য অনেকে ভুলে যান। অন্যদিকে উদ্ভিদের জীবনের বহিঃপ্রকাশের কারণে তিনি সেই দিকে বেশি কার্যকরী হন।
বর্তমানে, বিশ্বের তাবত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে জগদীশ চন্দ্র বসু কাজ করেছেন মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে এবং রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবক মার্কনি কাজ করেছেন বেতারতরঙ্গ নিয়ে।
অনেকেরই ধারণা, জগদীশ চন্দ্র যদি মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে তাঁর কোহেরারকে আরও এগিয়ে নিতেন, তাহলে ১৯০১ সালের প্রথম নোবেল পুরস্কারটি একজন বাঙালি পেলেও পেতে পারতেন। যে কলেজ তাঁকে নিয়োগ দিতে চায়নি, সে কলেজই তাঁকে অবসরের পরও অতিরিক্ত দুই বছর জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে বেতন দিয়েছে। ১৯১৫ সালে অবসরের পর তাঁকে প্রফেসর ইমেরিটাস মর্যাদা দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৩ সালে তাঁকে কমান্ডার অব ইন্ডিয়ান এমপায়ার উপাধি দেয়। ১৯২৮ সালে তিনি রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির ফেলো নির্বাচিত হন।
১৯২৭ সালে তিনি কলকাতায় একটি বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এটিকে তিনি একটি ‘মন্দির’ হিসেবে উল্লেখ করেন। বর্তমানে এটি বসু বিজ্ঞান মন্দির নামেই বেশি পরিচিত।
আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্র বসুর তিন বছরের ছোট হলেও তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল আমৃত্যু। একজনের হাতে বিকশিত হয়েছে বাংলায় সাহিত্য আর একজন করেছেন বাংলায় বিজ্ঞান রেনেসাঁর সূচনা।
স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একটি চমত্কার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, সে-ই প্রকৃত বিজ্ঞানী যে তার ল্যাবরেটরির সঙ্গে ঝগড়া করে না। অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানী সব সময় নিজের ল্যাবরেটরি তৈরি করে নেন, অন্যকে দোষারোপ করেন না।
আজ থেকে প্রায় সোয়া শ বছর আগে একটি পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে জগদীশ চন্দ্র বসু মানবসভ্যতাকে একটি বড় ঝাঁকুনি দিয়েছেন। সেই মাত্রায় না হলেও যদি আমরা তাঁর মতো বিজ্ঞানকে ভালোবেসে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাহলেই কেবল এই বিজ্ঞানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারব।
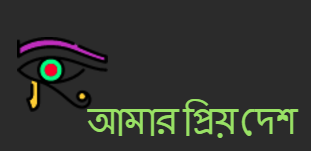

 Wormhole, in Interstellar
Wormhole, in Interstellar













