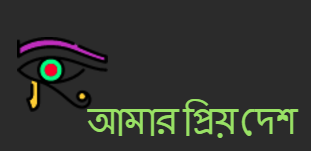কার্ল সেগানের “ভুয়া জ্ঞান সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া”
১৯৯৬ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের The Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark এর মাধ্যমে আমাদের জনপ্রিয় ছদ্মজ্ঞান আর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রণ কৌশল শিখিয়ে দেন।

উক্ত বইয়ের The Fine Art of Baloney Detection অধ্যায়ে আমাদের মাঝে প্রচলিত প্রচারণা- ধর্মীয় অপবিজ্ঞান- বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যাসহ বিজ্ঞানীদের ব্যবসায়ী প্রবণতা যাকে সেগান বলতেন- “ক্রেতাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতারণা” আর “বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখা দুর্নীতি”।
তবে তাঁর এই শিক্ষা নৈতিকতা আর স্বচ্ছচিন্তার সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে আসেনি- এসেছে তাঁর আবেগী অবস্থান- প্রিয় পিতামাতার প্রয়াণের পর। তিনি আমাদের বলেছেন আবেগের তাড়নায় মৃত্যু পরর্বতী জীবনে বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীনতার কথা- তিনি বলেছেন এতে আমরা বোকা হয়ে যাই না-শুধু আমাদের নিজেকে এসব ভিত্তিহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তৈরি রাখা।
বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অপবিজ্ঞান আর মিথ্যাপ্রচারণার বিরুদ্ধে এসব হাতিয়ার ব্যবহার করা শেখেন- সেগান এই হাতিয়ার গুলোকে বলেন- “ছদ্মবিজ্ঞান সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া”।
“এই হাতিয়ার কাজে লাগে তখনি যখন নতুন কোনো ধারনা আমাদের সামনে আসে। নতুন সেই ধারনা যদি আমাদের ছদ্মবিজ্ঞানরোধী ব্যবচ্ছেদের পরও বেঁচে থাকে তবে আমরা তাকে স্বাগত জানাবো। আপনি যদি কোন ভুল না করতে চান- অথবা বোকা না বনতে চান- তবে-পরিক্ষীত ভোক্তাবান্ধব এই অস্ত্র ব্যবহার আপনার শিখতে হবে।”
তবে এই প্রক্রিয়া, সেগান বলেন, শুধু বিজ্ঞানের জন্যই মোক্ষম হাতিয়ার না। আপনি চাইলেই দৈনন্দিন জীবনেও এর ব্যবহারের সুফল পাবেন। এই প্রক্রিয়া জানা থাকলে আপনি প্রমাণহীন ভুলধারনা কিংবা উদ্দেশ্যপ্রনোদিত মিথ্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। সেগানের মতে, এর ৯টি মূলনীতি হচ্ছে-
১) সম্ভবপর হলে সকল “ফ্যাক্টের” স্বাধীনসত্ত্বা থাকতে হবে, কোন “ফ্যাক্ট” অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল হতে পারবে না।
২) প্রাপ্ত প্রমাণের উপর ভিন্ন মতাদর্শের বিষয়গত বিতর্ক হওয়া উচিত।
৩) “কর্তৃপক্ষের মত” কোন মূল্য বহন করে না। “কর্তৃপক্ষরা” অতীতে ভুল মত দিয়েছেন, ভবিষ্যৎেও যে ভুল মত দিতে পারেন না এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। বিজ্ঞানে কোন কর্তৃপক্ষ নেই, বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ আছে।
৪) একের বেশী তত্ত্ব নিয়ে কাজ করুন। ব্যাখ্যাযোগ্য ব্যাপারের একের বেশী ব্যাখ্যা বিবেচনায় রাখুন। কোন কোন পরীক্ষা করে আপনি অন্য ব্যাখ্যাগুলোকে ভুল প্রমাণ করতে পারবেন সেটা ভাবুন। যাই বাঁচে- যে ব্যাখাই এই “ডারউইনিয় নির্বাচনে” টিকে থাকে তার সঠিক হওয়ার সম্ভাব্যনা- পছ্ন্দসই একটা ব্যাখার সঠিক হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে ঢের বেশী।
৫) নিজের তত্ত্ব বলে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন না। জ্ঞানের যাত্রাপথে আপনার তত্ত্ব একটা স্থান মাত্র। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কেনো আপনার তত্ত্ব আপনার পছন্দ, বিকল্পগুলোর সাথে আপনার তত্ত্বের তুলনা করে দেখুন। দেখুন তত্ত্বটিকে ভুল সাব্যস্ত করার কোন পথ খুঁজে পান কি না, আপনি না পেলেও অন্যরা ঠিকই পাবে।
৬) হিসাব যোগ করুন। আপনি যা ব্যাখ্যা করতে চান সেটা ব্যাখ্যা করা সহজ হবে যদি আপনি সেটাকে গানিতিকভাবে মাপতে পারেন। বিকল্পগুলোর মাঝে সবচেয়ে ভালোটার দিকে ইঙ্গিত করতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে। অবশ্যই এমন ব্যাপার আসবে যেখানে সংখ্যার চেয়ে গুনগতমান বিবেচনা করতে হতে পারে- কিন্তু সে ব্যাপারগুলো খুঁজে বের করা কঠিন হবে।
৭) যদি ধারণা/তত্ত্বটি দুই বা ততোধিক বিবেচ্য নির্ভর হয় তবে প্রত্যেকটি বিবেচ্য ব্যাখ্যাযোগ্য হতে হবে- অধিকাংশ বিবেচ্য ব্যাখ্যাযোগ্য হলেই চলবে না।
৮) অকাম’স রেজর। দুইটি সমান কার্যকরী ব্যাখ্যার মধ্যে সহজতর ব্যাখ্যা যা আরো প্রশ্নের জন্ম দেয় না, সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে।
৯) নিদেনপক্ষে, তাত্ত্বিকভাবে, আপনার তত্ত্ব বিকৃত করা যায় কি না প্রশ্ন করুন। যে ধারণা ভুল প্রমাণ করা যায় না, বিকৃত করা যায় না, সেই তত্ত্বের মূল্য কম। ধরুন- দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সবকিছু প্রাথমিক কণা- ইলেকট্রনের তৈরী- যদি বিরাট কসমসের ক্ষেত্রে এ ধারণা ব্যক্ত করা হয়? আমরা যদি দৃশ্যমণ মহাবিশ্বের বাইরেই না যেতে পারি তবে এই ধারণা কি ভুল প্রমাণের অযোগ্য না? সংশয়বাদীরা যেন পরীক্ষা করার সুযোগ পায়- আপনার মত একই ফলাফল পায়- এমন ব্যাখ্যা সৃষ্টি করুন।
এই কৌশলগুলো রপ্ত করার পাশাপাশি পূর্ববর্তী “জ্ঞান” দিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করার প্রবণতা বাদ দেয়ার কথাও সেগান বলেছেন। সেগান আমাদের মনে করিয়ে দেন ঠিক কোথায় আমরা এই কান্ডজ্ঞান বহির্ভূত কাজগুলোর প্রতি ঝুকে পড়ি।
“যে কোনো ছদ্মজ্ঞান সনাক্তকারী প্রক্রিয়া আমাদের কি করতে হবে শেখানোর পাশাপাশি কি করা যাবেনা সেটাও শেখায়। এটা আমাদের যুক্তি আর বাগ্মীতার দুই সর্বোচ্চ প্রচলিত ভ্রমের শিক্ষা দেয়- এর ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় ধর্মীয় আর রাজনৈতিক পরিমন্ডলে, কারণ এদের পালনকারীরা প্রায়শই দুইটা পরস্পরবিরোধী মতামতকে ন্যায়সঙ্গত করতে চেষ্টা করে।”
তিনি এরকম ২০টি বহুল প্রচলিত আর বিপজ্জনক মতামত যা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকে সেগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করেছেন-
১) ad hominem “ব্যক্তিকে” এর ল্যাটিন প্রতিশব্দ। বক্তৃতাকে না আক্রমণ করে বক্তাকে আক্রমণ করা।
যেমন-রেভারেন্ড ডাঃ স্মিথ একজন বাইবেল বিশেষজ্ঞ, বিবর্তনতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর মতামত আমলে নেয়ার কোন কারণ নাই।
২) argument from authority-
যেমন-রিচার্ড নিক্সনকে পুনর্নির্বাচন করা হয়েছে কারণ দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে তাঁর গোপন পরিকল্পনা ছিল। যেহেতু সেটা গোপন পরিকল্পনা, তাই এর উপকারিতা বিচারের কোন পথ নাই।
তাঁর রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্তটা পরে ভুল হিসেবে প্রকাশ পায়।
৩) argument from adverse consequences-
যেমন- শাস্তি এবং পুরস্কার প্রদানকারী ঈশ্বর অবশ্যই আছে- তা না হলে সমাজে অনৈতিকতা আরো বেড়ে যেত।
অথবা,
বহুল জনপ্রিয় হত্যামামলায় অভিযুক্তরা দোষী হোক বা নির্দোষ হোক, তাদের দোষী সাব্যস্ত করতেই হবে- তা না হলে মানুষ তাদের স্ত্রীদের হত্যা করার উৎসাহ পাবে।
৪) Appeal to ignorance- অসত্য প্রমাণ করা হয় নি, বিধায় কোনোকিছুকে সত্য ধরে নেয়া।
যেমন- UFO আসে না এর কোন প্রমাণ না থাকা প্রমাণ করে UFO আছে। আর মহাবিশ্বে অন্য বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণী আছে।
অথবা,
মহাবিশ্বে যদিও ৭০ “ক্যাজিলিয়ন” গ্রহ আছে, তবুও যেহেতু অন্য কোনো সভ্যতার প্রমাণ নাই সেহেতু আমরাই মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণী।
আমাদের অস্থিরতা থেকে আমরা প্রমাণ না থাকাকে না থাকার প্রমাণ ধরে নিয়েছি।
৫) special pleading প্রায়শই একটা গভীর বাগ্মী বিপদ থেকে বাঁচায়।
যেমন-কিভাবে পিতা-পুত্র এবং পবিত্র আত্মা তিনটি জিনিস কিভাবে এক ব্যক্তি হতে পারেন?
Special Pleading- তুমি Trinity এর ঐশ্বরিক রহস্য বোঝো নি।
অথবা
পরম দয়ালু সবজান্তা ঈশ্বর কেন একজন নারীর (ঈভ) অবাধ্যতার শাস্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেন?
Special Pleading- তুমি স্বাধীনচিন্তার বিষয়টি বোঝো নি।
৬) begging the question উত্তর অনুমান করে নেয়াও বলা হয় একে।
যেমন-সহিংস অপরাধ কমাতে মৃত্যুদন্ড চালু করতে হবে।
সেটা করলে যে সহিংস অপরাধ কমে যাবে সে উত্তর অনুমান করে নেয়া হয়েছে।
৭) Observational Selection পছন্দসই ফলাফলকে উপস্থাপন করা। দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের ভাষায়- “রাষ্ট্র সবসময় উৎপাদিত রাষ্ট্রপতিতের ব্যাপারে গর্ব করে- উৎপাদিত খুনিদের ব্যাপারে রাষ্ট্র কথা বলে না।
৮) Statistics of small numbers- Observational Selection এর মত-
যেমন- প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে গড়ে একজন মানুষ চাইনিজ হয়। সেটা কিভাবে সম্ভব- আমি শত শত লোককে চিনি, তাদের কেউই চাইনিজ নন।
৯) Misunderstanding the nature of statistics-
যেমন- অর্ধেক আমেরিকানদের বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিকের চেয়ে কম- এই পরিসংখ্যানে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়্যারের বিস্ময় প্রকাশ করা।
১০) Inconsistency
যেমন- মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কাল অসীম হওয়ার সম্ভাব্যতাকে মেনে নেয়া তবে অসীম অতীত কালের সম্ভাব্যতাকে অযৌক্তিক মনে করা।
১১) Non sequitur- “it doesn’t follow” এর ল্যাটিন পরিভাষা।
যেমন- আমাদের দেশই উন্নত হবে কারণ মহান ঈশ্বর আমাদের পক্ষে, অথচ সকল দেশই এটা ভাবে। (যারা non sequitur এ পড়েন তারা সাধারণত বিকল্প সম্ভাবনাগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকেন না।)
১২) post hoc, ergo propter hoc- ‘ক’ ঘটনা ‘খ’ ঘটনার আগে ঘটেছে সুতরাং ‘খ’ ঘটনার কারণ ‘ক’ ঘটনা।
যেমন- জ্যামি কার্ডিনাল সিন, ম্যানিলার আর্চ বিশপ বলেন- “আমার পরিচিত এক ২৬ বছর বয়স্কা আছেন যাকে দেখতে ৬০ বয়স্কা মনে হয়- কারণ তিনি জন্মনিয়ন্ত্রন বড়ি সেবন করেন।
অথবা,
নারীরা ভোটাধিকার পাওয়ার আগে পারমানবিক অস্ত্র ছিল না।
১৩) meaningless question-
যেমন- যদি অপ্রতিরোধ্য কোন শক্তি অনড় কোন বস্তুকে আঘাত করে তবে কি ঘটবে?
(যদি অপ্রতিরোধ্য কোন শক্তি থেকে থাকে তবে অনড় কোন বস্তু থাকতে পারবে না, এবং উল্টোটাও একইভাবে সম্ভাব্য।)
১৪) Excluded middle or False Dichotomy – আলোচ্য বিষয়কে দুটোমাত্র সম্ভাব্যতায় আবদ্ধ করা।
যেমন- হয় তুমি তোমার দেশকে ভালোবাসো, আর না হয় ঘৃণা করো। *
অথবা,
হয় তুমি সমাধানের অংশ না হয় তুমি সমস্যার অংশ।
১৫) Short term vs Long term- excluded middle এর গুরুত্বপূর্ণ উপপর্যায়- এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটাকে আলদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে।
যেমন- অপুষ্টি আর শিক্ষাহীনতায় ভোগা শিশুদের চেয়ে তৃনমূল থেকে অপরাধ মোকাবেলা করা আমাদের বাজেটবান্ধব হবে।
অথবা,
আমাদের বাজেটের ঘাটতি বিবেচনা করে মহাশূন্য গবেষণা আর মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা করাটা মূখ্য মনে হয় না।
১৬) Slippery slope – excluded middle এর সাথে সম্পর্কিত।
যেমন- যদি প্রথম সপ্তাহে ভ্রূনের গর্ভপাত করা হয় তবে পূর্ণবয়স্ক অভূমিষ্ঠ শিশুহত্যা রোধ করা যাবে না।
অথবা,
যদি নবম মাসেও আমাদের গর্ভপাত করতে না দেয়া হয় তবে কিছুদিন পর আমাদের অন্তঃস্বত্তা হওয়াকালীন দৈহিক ব্যবহারও সরকার বলে দিবে।
১৭) Confusing correlation and causation-
যেমন- এক সমীক্ষা বলে সমকামিদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতদের আধিক্য আছে আর অল্প শিক্ষিতদের মাঝে সমকামিদের সংখ্যা কম- সুতরাং উচ্চশিক্ষা সমকামিতার কারণ।
১৮) Straw man বা বক্তব্যের মনগড়া ব্যাখা দিয়ে আক্রমন সহজ করা।
যেমন- বিজ্ঞানীরা মনে করেন সবকিছু দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এটা ডারউইনিও নীতি মেনে সম্ভব না, কারণ সেটা বলে প্রকৃতি কর্মক্ষম সবকিছুকে টিকিয়ে রাখে আর অকর্মণ্য সবকিছুকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।
অথবা,
এটাকে short term vs long term হেত্বাভ্যাসও বলা যায়- পরিবেশবাদীরা মানুষের চেয়ে পেঁচা আর শামুকের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল।
১৯) Suppressed evidence or half truths
যেমন- রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানকে হত্যা করার পর টেলিভিশনে এক ব্যক্তির চমকপ্রদ ভবিষ্যৎবানী প্রচারিত হয় যা বলে রেগানকে কিভাবে হত্যা করা হবে।
(তবে চিত্রায়ণের তারিখ ছাড়া সকল তথ্যই সঠিকভাবে বলা হয়েছিল। )
অথবা,
সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে- ডিম না ভেঙ্গে অমলেট বানানো যায় না।
(হ্যাঁ, তবে এই বিদ্রোহ কি সবার জন্য ভাল হবে? এটা কি সরকারী শোষণের তুলনায় কম রক্তক্ষয়ী হবে? অভিজ্ঞতা থেকা পাওয়া জ্ঞান কি তার সায় দেয়?)
২০) Weasel words
যেমন- আমেরিকার সংবিধানে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা কংগ্রেসের কাছে ন্যস্ত, যাতে রাষ্ট্রপতিরা যুদ্ধ শুরু না করতে পারেন। তবে পররাষ্ট্রনীতি আর যুদ্ধনীতি রাষ্ট্রপতির মর্জি নির্ভর হয়। রাষ্ট্রপতিরা দেশপ্রেমের আড়ালে ভিন্ননামে যুদ্ধ শুরু করতে পারেন- যেমন- “পুলিশী কর্মকান্ড”, “অস্ত্রসজ্জিত আকস্মিক আক্রমন”, “রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ায় আক্রমন”, “শান্তকরন”, “আমেরিকার স্বার্থরক্ষা”। যুদ্ধের এসব প্রতিশব্দ ব্যবহার করা রাজনৈতিক কারণে ভাষাকে ব্যবহার করার নজীর । Talleyrand বলেন- “রাজনীতিবিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা কলা হচ্ছে নতুন নামে পুরোনো এবং জনস্বার্থবিরোধী কাজ করার পথ খুঁজে নেয়া।”
সেগান একটা সতর্কবাণী দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করেন-
“সব অস্ত্রের মত এই ছদ্মজ্ঞান সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ারও অপব্যবহার আছে- প্রাসঙ্গিকতার বাইরে ব্যবহার করা- অথবা চিন্তা করার বিকল্প হিসেবেও একে ব্যবহার করা যায়। নিজের মত অন্যকে জানানোর আগে নিজে যাচাই করে নেয়া ছাড়াও বিজ্ঞ ব্যবহারে এই প্রক্রিয়া পৃথিবী বদলে দেয়ার ক্ষমতাও রাখে।”
The Demon Haunted World বইটি একটি কালজয়ী রচনা। এর বিষয়বস্তু যেন এই ছদ্মবিজ্ঞান আর অপপ্রচারের যুগের জন্যই সেগান লিখে গিয়েছিলেন।
উৎস ঃ http://onubadokderadda.com/baloney_detection/