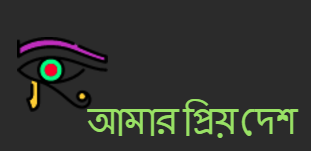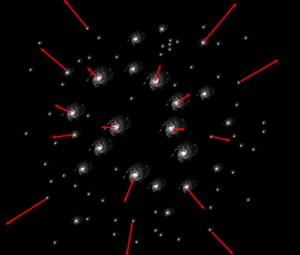হুমায়ূনকে আমি প্রথম দেখি একুশের বইমেলায়, সাতাশি সালের এক সন্ধ্যায়।
যিনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘‘ইনি হুমায়ূন আহমেদ। ‘এইসব দিনরাত্রি’ নামে একটি জনপ্রিয় টিভি-নাটক লিখেছেন, ‘শঙ্খনীল কারাগার’ নামের উপন্যাস লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ান।’’
দেখলাম, একটি শীর্ণ যুবককে, যার পরনে পা়ঞ্জাবি, চোঙা পাজামা গোড়ালির ওপরে। কিন্তু চশমার আড়ালে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। হেসে বলেছিল, ‘‘আমি আপনাদের লেখা পড়ে বড় হয়েছি।’’
সে দিন মেলার দর্শক-শ্রোতারা হুমায়ূনকে ঘিরে ভিড় জমায়নি। রথের মেলায় উদাসীন বালকের মতো বইমেলায় ঘুরছিল সে।
বছর পাঁচেক পরে ঢাকার একুশের বইমেলায় ঢুকেই দেখি বিশাল লাইন। বই হাতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রশ্ন করে জানলাম ওঁরা হুমায়ূন আহমেদের বই কিনে দাঁড়িয়ে আছেন অটোগ্রাফ করিয়ে নেবেন বলে। অন্তত পাঁচ-ছ’শো মানুষ একই আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন দেখে অবাক হলাম।
আমাদের কলকাতা বইমেলায় এমন ঘটনা ঘটেছে কি না মনে পড়ল না। সমরেশ বসু-শংকর-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা যখন মেলায় আসতেন, তখন তাঁদের ঘিরে ছোটখাট ভিড় জমলেও এমন লাইন পড়ত না।
সময়টা উনিশশো বিরানব্বই। তখনও কলকাতার পাঠকদের নব্বই ভাগ হুমায়ূন আহমেদের নাম শোনেননি, বই পড়া তো দূরের কথা। লাইনের শুরুতে পৌঁছে দেখলাম একটি স্টলের সামনে চেয়ারে বসে হুমায়ূন মাথা নিচু করে একের পর এক সই দিয়ে যাচ্ছে। যে বই এগিয়ে দিচ্ছে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না।
আমি একটা ‘গীতবিতান’ এগিয়ে ধরতে সে আমাকে না দেখে বইটি নিল। সই করার ঠিক আগে থেমে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘‘সর্বনাশ, আপনি কি আমাকে দোজখে পাঠাতে চান? এই বই-এ সই করার যোগ্যতা তো আমার—!’’ বলতে বলতে মুখ তুলেই সে আমাকে দেখতে পেল। তার চোখ বিস্ফারিত হল। লাফিয়ে উঠে আমাকে প্রণাম করতে এল সে। বলল, ‘‘ছি ছি, আপনি আমায় এ কী লজ্জায় ফেললেন!’’
গত পঞ্চাশ বছরে আমি বিখ্যাত, অতি বিখ্যাত অনেক লেখকের সংস্পর্শে ধন্য হয়েছি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মুখে ওঁর কথা শুনেছি। ওরকম নির্লোভ, সরল লেখকের সঙ্গে হুমায়ূনের মিল পেয়েছি। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে যে বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমরা গর্ব করি, তার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকের নাম হুমায়ূন আহমেদ।
চুরানব্বই সালের একুশের মেলার শেষে শোনা গেল, ওঁর সমস্ত বই এক মেলায় কত কপি বিক্রি হয়েছে, তার হিসেব নেই, তবে নতুন বইগুলোর বিক্রির সংখ্যা পঁচিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতা বইমেলায় যদি কারও দেড়-দু’হাজার বই বিক্রি হয়, তা’হলে তাঁকে আমরা জনপ্রিয় লেখক বলি। হুমায়ূনের সঙ্গে তুলনা করার কথা চিন্তাও করা যায় না।
তখনও পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ পাঠক ওঁর কথা জানে না। যখন ওঁর একটি টিভি নাটকের চরিত্র, যাঁকে নাটকেই ফাঁসি দেওয়া হবে জেনে হাজার হাজার দর্শক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিল, সে দিন পশ্চিমবাংলার কাগজে সেটা খবর হয়েছিল। এরকম হয় নাকি? বিস্ময় ছিল অনেকের।
কলকাতার এক নামী প্রকাশক আমার মাধ্যমে যোগাযোগ করে অনুমতি নিয়ে ওর বিখ্যাত কয়েকটি বই ছাপলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, কুড়ি বছর আগে পশ্চিমবাংলায় বইগুলো পাঠক পায়নি। অথচ ঢাকায় বিক্রি হয়েছিল রমরমিয়ে।
হুমায়ূন বয়সে আট বছরের ছোট হলেও বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল। ওর স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছি অনেকবার। হুমায়ূনের বাসনা ছিল চলচ্চিত্র তৈরি করার। অনেকগুলো ছবি তৈরি করেছিল সে। প্রথম দিকের একটি টেলি প্লে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল আমাকে। দেখতে দেখতে আমার ঘুম পাচ্ছিল। সে ওটা বন্ধ করে বলেছিল, ‘‘বুঝতে পারছি কিছুই হয়নি। হলে আপনার ঘুম পেত না।’’
যখনই ঢাকায় গিয়েছি, সন্ধে থেকে মধ্যরাত হুমায়ূনের সঙ্গে কেটেছে। এই রকম এক রাতে সে আমাকে বলল, ‘‘সমরেশদা, আমার বহুকালের ইচ্ছে দেশ পত্রিকায় উপন্যাস লিখব। আপনি দয়া করে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন?’’
‘‘কেন এমন ইচ্ছে হল?’’ জিজ্ঞেস করেছিলাম।
‘‘যে কাগজে রবীন্দ্রনাথ থেকে আপনারা লিখেছেন, সেখানে না লিখলে নিজেকে ঠিক—,’’ হুমায়ূন হেসেছিল।
‘‘কিন্তু হুমায়ূন, এখানে একজন প্রকাশক তোমাকে দশ লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে অপেক্ষা করে কখন পাণ্ডুলিপি দেবে, আমাকেই অনেকে দুঃখ করে বলেছে যে তোমার একটা উপন্যাসের আশায় কয়েক বছর ধৈর্য ধরে আছে। কলকাতার কাগজে লিখলে তুমি যা পাবে তা তো তুলনায় আসবে না।’’
‘‘না, সমরেশদা, দেশ পত্রিকার বিকল্প হয় না। দেশ ইজ দেশ।’’
হুমায়ূন কলকাতায় এলে সাগরময় ঘোষ মশাই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সে অত্যন্ত বিনীত গলায় বলেছিল, ‘‘আমাকে যদি লেখার সুযোগ দেন।’’
সাগরদাও বলেছিলেন, ‘‘দেখি!’’
তারপর বেশ কয়েক বছর হুমায়ূন দেশ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় একের পর এক উপন্যাস লিখে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার পাঠক সেই সব উপন্যাস নিয়ে কোনও হইচই করেননি, কিন্তু ঢাকার প্রকাশকরা দশ-বারো লক্ষ টাকা আগাম দিয়ে সেগুলো একুশের মেলাতেই তিরিশ হাজার কপি বিক্রি করেছে।
এক বন্ধু খবরটা দিয়েছিলেন যে হুমায়ূন চট্টগ্রামের কাছে সমুদ্রে একটি দ্বীপ কিনেছেন। শুনে অবাক হয়েছিলাম। কোনও বাঙালি লেখকের পক্ষে কি দ্বীপ কেনা সম্ভব? সেই দ্বীপ কিনে লেখক করবেই বা কী?
দেখা হতেই হুমায়ূনকে জিজ্ঞাসা করতে সে সলজ্জ হাসল, ‘‘আমি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে একটি বাড়ি কিনেছি। এমন কিছু ব্যাপার নয়। আসুন না একবার, সামনের ডিসেম্বরেই আসুন, ঘুরে আসি।’
‘‘বর্ষাকালে যাওয়া যায়?’’
‘‘যায়। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। দ্বীপের অনেকটাই জলের তলায় থাকে। শীতে জল নেমে গেলে বাসযোগ্য হয়,’’ হুমায়ূন বলেছিল।
‘‘বাড়িটা কিনেছিলে কেন?’’
‘‘সমুদ্রের মধ্যে বাড়িতে থাকলে খুব মজা লাগে সমরেশদা।’’
গোটা দ্বীপ অবশ্যই নয়। দ্বীপের মধ্যে একটি বাড়ি কিনে যে মানুষ মজা পায়, সে যে জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।
টাকা যেন হুমায়ূনকে তাড়া করত। বাংলাদেশের অন্যান্য নাট্যকারের কল্পনার বাইরে সম্মানদক্ষিণা হুমায়ূনকে দেওয়া হত। বলা ভাল দিতে বাধ্য হতেন প্রকাশকরা। কারণ সেই সব নাটকের দর্শক সংখ্যা ছিল বিপুল। অথচ হুমায়ূনের চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক দেখলে মনে হত, পাশের বাড়ির ছেলে যার কোনও অহঙ্কার নেই।
স্ত্রীর সঙ্গে মতান্তর হচ্ছে ওর, খবর পেয়েছিলাম। ঔৎসুক্য দেখাইনি। খারাপ লাগলেও মনে হয়েছিল, এটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।
সে সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। আনন্দবাজারের পুজো সংখ্যায় ‘এত রক্ত কেন’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের নিয়ে যারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিত, তাদের নিয়ে। সেই পুজো সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করেছিল বাংলাদেশ সরকার।
এই সময় হুমায়ূন আহমেদ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় ওর এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য।
ঢাকা বিমানবন্দরে পুলিশ আমায় আটক করে। এবং শেষ পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে বাইরে যেতে দেয়। সেটা হল আমি ঢাকা শহরে থাকতে পারব না। হুমায়ূন সোজা আমাকে ঢাকা থেকে অনেক দূরে তার নুহাসপল্লিতে নিয়ে যায়। কয়েক একর বাগানঘেরা জমিতে সে তার ফিল্মশ্যুটিং-এর স্টুডিয়ো বানিয়েছিল। গেস্টহাউসে ঘরও অনেকগুলো।
হুমায়ূন এবং তার সর্বক্ষণের সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডা মারার সময় সন্ধের মুখে বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি। বাইরে ঘন অন্ধকার। গাছগুলো যে ঝড়ে দুলছে তা টের পাচ্ছি। লেখালেখি নিয়ে কথা উঠতে হুমায়ূন হাসল, ‘‘আমার কথা ছাড়ুন। বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা। আসলে কী জানেন, পাকিস্তান আমলে কলকাতা থেকে বাংলা বই আসা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাঠক নতুন বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। আমাদের এখানে যাঁরা প্রতিভাবান সিরিয়াস লেখক, তাঁদের লেখা সমালোচকদের শ্রদ্ধা পেলেও আমপাঠক খুশি হতে পারছিলেন না। যাঁরা নীহাররঞ্জন, অবধূত, প্রবোধ সান্যাল পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। যাঁরা সমরেশ বসু পড়তেন, তাঁরা আর কত পুরনো বই পড়বেন! হয়তো আমার লেখায় সেই ধরনের রোম্যান্সের স্বাদ পেলেন এঁরা, যা চেয়েছিলেন। আমি কখনই তারাশংকর, বিভূতিভূষণ বা সমরেশ বসুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারব না। আমাকে যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা বলেন, পনেরো-ষোলোতে যাঁরা হুমায়ূন পড়া শুরু না করে, তারা পাঠক নয়। আবার চব্বিশের পরে যারা হুমায়ূন পড়ে তাদেরও ভাল পাঠক বলা যায় না। আমি এখনও রবীন্দ্রনাথ পড়ি আর প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখি।’’
হুমায়ূনের বেশির ভাগ বইয়ের নামকরণ সে করেছে রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন থেকে শব্দ নিয়ে। এমনকী নিজের তৈরি ছবির নাম রেখেছিল ‘আগুনের পরশমণি’। নিজের লেখা নিয়ে সে সব সময় বিনীত ছিল।
সেই বৃষ্টির রাত্রে, প্রায় দশটার মধ্যে, এক হাঁটু জল ভেঙে একটা গোরুর গাড়ি এল নুহাসপল্লিতে। সম্পূর্ণ ভিজে এক তরুণী নেমে এল গোরুর গাড়ি থেকে, নেমে হুমায়ূনকে অনুযোগ করল বড় রাস্তার মোড়ে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করেনি বলে।
মেয়েটি পোশাক পাল্টাতে বাথরুমে গেলে হুমায়ূন সলজ্জ হাসল, ‘‘ওঃ, খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।’’ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘‘মেয়েটি কে? এ ভাবে কথা বলল?’’
‘‘ওঁর নাম শাওন, অভিনয় করে। ভাল গান গায়।’’ এর বেশি বলেনি সে।
হুমায়ূনের বিবাহবিচ্ছেদ এবং শাওনের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে ওর পাঠক-পাঠিকাদের দুঃখিত করেছিল। আমাকে এ কথা অনেকেই বলেছেন। শাওন বয়সে ওর মেয়ের মতো, রক্ষণশীলরা মেনে নিতে পারেননি। সবাই আশঙ্কা করেছিলেন এই ঘটনার ফলে হুমায়ূন জনপ্রিয়তা হারাবে, তার বই বিক্রি দ্রুত কমে যাবে। প্রথম দিকে সে রকম মনে হলেও দেখা গেল হুমায়ূনের পাঠক কমে গেল না। লেখকের ব্যক্তিজীবন আর তাঁর লেখাকে গুলিয়ে ফেললেন না পাঠকরা।
হুমায়ূনের সঙ্গে ঢাকা বা কলকাতা ছাড়া দেখা হয়েছে আমেরিকায়। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি, বাংলাদেশের মানুষ আর কোনও বই রাখুক বা না রাখুক, হিমু বা মিসির আলি রেখেছে। এই দুটি চরিত্র লিখে হুমায়ূন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। হিমুর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদকে অনেকেই খুঁজে পান। আমার ভাল লেগেছে মিসির আলিকে।
দেশবিদেশের অনেক গোয়েন্দা গল্প আমি পড়েছি। কিন্তু এমন কোনও গোয়েন্দার খবর পাইনি যিনি পেটের গোলমালে ভোগেন। যাঁর কাছে কোনও ক্লায়েন্ট এসে কথা শুরু করার সময় মিসির আলিকে যদি পটি করতে ছুটতে হয় তা’হলে তার পরে আধঘণ্টা না শুয়ে থাকলে কাজ করার উৎসাহ পান না। অপেক্ষা করে করে ক্লায়েন্ট চলে গেলেও মিসির আলি নিয়ম ভাঙেন না। কিন্তু তদন্তে নেমে তিনি যে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ করতে সক্ষম, তার তুলনা খুব কম পাওয়া যাবে।
নিউইয়র্কের কুইন্সের এক হোটেলে আমরা ছিলাম। গিয়েছিলাম এক বইমেলায় অংশ নিতে। রাত্রে আড্ডা হচ্ছিল। সে হেসে বলেছিল, ‘‘যাই বলুন সমরেশদা, পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের চেয়ে বাংলাদেশের পাঠক অনেক উদার। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সৈয়দ মুজতবা আলী আর কিছুটা সিরাজভাই ছাড়া আর কোনও মুসলমান লেখককে সেখানকার হিন্দু পাঠক গ্রহণ করেননি। মুজতবা আলী সাহেব গীতা, চণ্ডী, বাইবেল, কোরান পড়ে নিজের মতো লিখেছেন। তাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি কেউ। তাছাড়া লেখায় যে রস ছিল, তা মোহিত করত সবাইকে। আমাদের লেখায় নামাজ, আপা, ফুপা, দুলাভাই, দোয়া, রোজা ইত্যাদি শব্দ থাকে বলে হিন্দু পাঠকদের বোধহয় অস্বস্তি হয়। কিন্তু আপনাদের লেখায় তুলসী মঞ্চ, শালগ্রাম শিলা, যাগযজ্ঞ থাকলেও মুসলমান পাঠক তা নিয়ে মাথা ঘামান না। তারা গল্পটাই পড়তে ভালবাসেন। আমি আশা করি, পরিস্থিতির বদল হবেই।
বলেছিলাম, ‘‘কথাটা এখনও পর্যন্ত ঠিক। এটা বোধহয় লেখা এবং পড়ার সময় দীর্ঘদিনের অভ্যেস প্রতিবন্ধকতার কাজ করে। পশ্চিমবাংলার বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকদের কলমে মুসলমান নায়ক-নায়িকা উপন্যাসে জায়গা পেয়েছে কি না এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। শরৎচন্দ্র গফুর চরিত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তাকে মানুষ হিসেবেই সবাই ভেবেছে। গফুরের গোরুর মুসলমান নাম রাখাটাই তো স্বাভাবিক হত। তবে এই অভ্যেস বদলাচ্ছে। কলকাতার অনেক তরুণতরুণী এখন হিমুর কথা পড়তে চায়। মুশকিল হল বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেও তোমাদের লেখায় উর্দু আরবি শব্দের প্রাধান্য আজকাল দেখা যাচ্ছে যার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার পাঠক আদৌ পরিচিত নয়। যেমন, জিম্মা।’’
হুমায়ূন হাসল, ‘‘আসলে ওই সব শব্দ শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি। তাই কলমে এসে যায়। আমি জল বলি, পানিও। কিন্তু লিখতে গিয়ে পানি লিখি। আপনি জল বলেন। কিন্তু জলে যে ফল জন্মায়, তাকে পানিফল বলেন।’’
পরের সকালে ঘটনাটি ঘটল। হুমায়ূন রাত্রে ঘুমোবার আগে তার ডলারভর্তি মানিব্যাগ বালিশের নীচে রেখে দেয়। সকালে উঠে দেখল সেটা নেই। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। পাওয়া গেল না।
হুমায়ূনের মুখ গম্ভীর। বলল, ‘‘আমি কপর্দকহীন।’’
কে নিতে পারে হাজার চারেক ডলার? বাইরের কেউ নেবে, এমন সম্ভাবনা নেই। ওর সঙ্গে যারা ছিল তাদের একজনই কাজটা করেছে। কিন্তু স্বীকার করছে না।
দুপুরে অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম, সে তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে বাইরের ফুটপাথে বসে আছে। হেসে বলল, ‘‘সমরেশদা, যে নিয়েছে সে যেন বিবেকের কামড় খেয়ে ফেরত দিতে না আসে। তা’হলে তাকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারব না। যে নিয়েছে তাকে আমি সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু আমার সন্দেহ তো সঠিক নাও হতে পারে। তাই তাকে অপরাধী ভাবছি না।’’
অদ্ভুত ব্যাপার! পরের দিনই হুমায়ূনের বালিশের নীচে মানিব্যাগটি পাওয়া গেল। একটি ডলারও খোয়া যায়নি। হুমায়ূন বলল, ‘‘যে নিয়েছে এবং ফেরত দিয়েছে তাকে ধন্যবাদ, কারণ ফেরত দেওয়ার নাটকটা করেনি।’’
খ্যাতির শিখরে উঠে লিখে প্রচুর অর্থ পেয়েও হুমায়ূনের ব্যবহার ছিল খুব সাধারণ। ঢাকায় গেলেই জিজ্ঞাসা করত, ‘‘সুনীলদা কেমন আছেন?’’ খুব ভক্ত ছিল সে সুনীলদার লেখার। বলত, ‘‘মানুষটার লেখা পড়তে বসলেই একটা অদৃশ্য হাত এসে ঘাড় ধরে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে নিয়ে তবে ছাড়ে।’’
বললাম, ‘‘লোকে এ কথা তোমার ক্ষেত্রেও বলে!’’
‘‘দূর!’’ হুমায়ূন বলেছিল, ‘‘আমি তো যা লিখতে চাই, তা লিখতে পারি না বলে এই সব লিখি। আমাদের লেখায় কেন সমকালীন রাজনীতির ছাপ থাকে না বলে আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উত্তরটা হল, লিখতে ভয়
করে।’’
হুমায়ূন তখনও অসুস্থ হননি। ঠিক তার আগে ঢাকায় যেতেই ওর ফোন এল, ‘‘সমরেশদা, আসুন, অনেক কথা আছে।’’
সন্ধের পর গিয়ে দেখলাম অনেক মানুষকে নিয়ে সে আড্ডা মারছে। লেখক, প্রকাশক, গায়ক, নায়ক কে নেই! পিনা এবং খানার সঙ্গে লক্ষ করলাম হুমায়ূন ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে। রাত বাড়তে উঠতে চাইলে সে হাত ধরল, ‘‘আপনার সঙ্গে কথা আছে। সবাই চলে যাক, তারপর—।’’
শাওন তার শিশুদের নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। অতিথিরা বিদায় নিলেন রাত সাড়ে বারোটায়। আমি আর হুমায়ূন চুপচাপ বসেছিলাম। বললাম, ‘‘বলো।’’
সে শ্বাস ফেলল শব্দ করে। বলল, ‘‘খুব কষ্ট হয় সমরেশদা। জীবনে যা চেয়েছি, তার অনেকটাই পেয়েছি। এই চাইতে গিয়ে অনেক কিছুই হারাতে হয়েছে। কী করি বলুন তো?’’
‘‘আমৃত্যু এই কাঁটা তোমার আমার সবার মনে বিঁধতে থাকবে। এই নিয়েই তোমাকে বাস করতে হবে। তোমার কাজটা তুমি করে যাও, কষ্টটা কমে যাবে।’’
সত্যি কি কষ্ট কমে? সত্যি কি ভুলতে চাইলে ভোলা যায়? আমার তো মনে হয় না। এর কিছু দিন পরে কর্কটরোগে আক্রান্ত হল হুমায়ূন। তা সত্ত্বেও সিগারেট ত্যাগ করল না। সে কি মৃত্যুকে দেখেছিল বলে মাথা নোয়ালো না? নিজের মতো করে চলে গেল?
মধ্য ষাটের সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন মানুষ, যিনি নিজে পাঠক তৈরি করেছেন, সেই পাঠকদের মনে বসত করেছেন, তিনি চলে গেলেও থেকে যাবেন। এটাই তো পরম পাওয়া।
উৎস ঃ
এখানে ক্লিক করুন ..